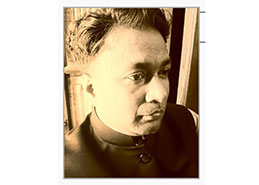
 পি.বি.
শেলীর জন্মের দুশো বিশ বছর পূর্ণ হলো। ১৭৯২ সালের ৪ঠা আগস্ট মাসে তাঁর
জন্ম। চার বছর আগে বায়রনের দুশো পঁচিশ বছর পূর্ণ হয়েছে। আর তিন বছর পরে
কিটসের দুশো বিশ বছর পূর্ণ হবে। ইংরেজি রোমান্টিক কাব্যের পুনরাবর্তন যুগ
(অমব ড়ভ জড়সধহঃরপ জবারাধষ) দুই পর্বে বিভক্ত। প্রথম পর্বে ওয়ার্ডসওয়ার্থ
কোলরিজ সাদে; দ্বিতীয় পর্বে বায়রন শেলী কিটস। কালের অবিরাম গতিতে শত বছর গত
হওয়াটা একটা মস্ত বড় কথা নয়। আসল প্রশ্নটা হলো, দুশো বছর পরে আজ শেলী
কতখানি বেঁচে আছেন। কালের গতিবেগের সব জিনিসেই ক্ষয়ক্ষতি, ভাঙচুর কিছু ঘটেই
থাকে। দেখতে হবে, কালের ঝাপটায় শেলীর কতখানি খোয়া গিয়েছে, কতখানি অবশিষ্ট
আছে। কালের খামখেয়ালিপনায় অটুট থাকে না কিছুই– ক্ষণে ক্ষণে রং বদলায়, ঢং
বদলায়। রবীন্দ্রনাথের মনে প্রশ্ন জেগেছিল, শতবর্ষ পরে চৌদ্দশ সালে যে পাঠক
বা পাঠিকা তাঁর কবিতা পাঠ করছেন, আজকের বসন্ত দিনের যে আনন্দ-আবেগে তাঁর
প্রাণ উদ্বেল তার কণাটুকুও কি তিনি তাঁর চৌদ্দশ সালের পাঠকের মনে সঞ্চারিত
করতে পারবেন? তবু এই মনোবাসনা উচ্চারণ করেছেন ‘আমার বসন্ত গান তোমার বসন্ত
দিনে/ ধ্বনিত হউক ক্ষণতরে।’ রবীন্দ্রনাথ এ প্রশ্নও তুলেছিলেন– আজ যাঁরা
তোমাদের কবি তাঁরা তোমাদের কী গান শোনাচ্ছেন কে জানে? শতবর্ষ পূর্ণ হয়ে
চৌদ্দশ সাল অতিক্রান্ত। দেখতেই পাচ্ছি, আজকের বাংলা কাব্য রবীন্দ্রনুরাগীর
নয়। দোষের কথা নয়। মানুষে মন বদলায়, রচি বদলায়, সেই সঙ্গে যুগ বদলায়। রুচির
আবার ঘুরে ঘুরে ফিরে আসে। ষোড়শ শতকে শেকসপিয়রের যুগে যে রোমান্টিক কাব্য
প্রচলিত ছিল, সেই রোমান্টিক কাব্যেরই পুনরাবির্ভাব ঘটেছিল– তিনশ বছর পরে
ওয়ার্ডসওয়ার্থ শেলী কিটসের যুগে ঊনবিংশ শতকে।
পি.বি.
শেলীর জন্মের দুশো বিশ বছর পূর্ণ হলো। ১৭৯২ সালের ৪ঠা আগস্ট মাসে তাঁর
জন্ম। চার বছর আগে বায়রনের দুশো পঁচিশ বছর পূর্ণ হয়েছে। আর তিন বছর পরে
কিটসের দুশো বিশ বছর পূর্ণ হবে। ইংরেজি রোমান্টিক কাব্যের পুনরাবর্তন যুগ
(অমব ড়ভ জড়সধহঃরপ জবারাধষ) দুই পর্বে বিভক্ত। প্রথম পর্বে ওয়ার্ডসওয়ার্থ
কোলরিজ সাদে; দ্বিতীয় পর্বে বায়রন শেলী কিটস। কালের অবিরাম গতিতে শত বছর গত
হওয়াটা একটা মস্ত বড় কথা নয়। আসল প্রশ্নটা হলো, দুশো বছর পরে আজ শেলী
কতখানি বেঁচে আছেন। কালের গতিবেগের সব জিনিসেই ক্ষয়ক্ষতি, ভাঙচুর কিছু ঘটেই
থাকে। দেখতে হবে, কালের ঝাপটায় শেলীর কতখানি খোয়া গিয়েছে, কতখানি অবশিষ্ট
আছে। কালের খামখেয়ালিপনায় অটুট থাকে না কিছুই– ক্ষণে ক্ষণে রং বদলায়, ঢং
বদলায়। রবীন্দ্রনাথের মনে প্রশ্ন জেগেছিল, শতবর্ষ পরে চৌদ্দশ সালে যে পাঠক
বা পাঠিকা তাঁর কবিতা পাঠ করছেন, আজকের বসন্ত দিনের যে আনন্দ-আবেগে তাঁর
প্রাণ উদ্বেল তার কণাটুকুও কি তিনি তাঁর চৌদ্দশ সালের পাঠকের মনে সঞ্চারিত
করতে পারবেন? তবু এই মনোবাসনা উচ্চারণ করেছেন ‘আমার বসন্ত গান তোমার বসন্ত
দিনে/ ধ্বনিত হউক ক্ষণতরে।’ রবীন্দ্রনাথ এ প্রশ্নও তুলেছিলেন– আজ যাঁরা
তোমাদের কবি তাঁরা তোমাদের কী গান শোনাচ্ছেন কে জানে? শতবর্ষ পূর্ণ হয়ে
চৌদ্দশ সাল অতিক্রান্ত। দেখতেই পাচ্ছি, আজকের বাংলা কাব্য রবীন্দ্রনুরাগীর
নয়। দোষের কথা নয়। মানুষে মন বদলায়, রচি বদলায়, সেই সঙ্গে যুগ বদলায়। রুচির
আবার ঘুরে ঘুরে ফিরে আসে। ষোড়শ শতকে শেকসপিয়রের যুগে যে রোমান্টিক কাব্য
প্রচলিত ছিল, সেই রোমান্টিক কাব্যেরই পুনরাবির্ভাব ঘটেছিল– তিনশ বছর পরে
ওয়ার্ডসওয়ার্থ শেলী কিটসের যুগে ঊনবিংশ শতকে।
এখানে একটি কথা বলে নেওয়া
যেতে পারে। এক সময়ে আমাদের দেশে একটি ছেলেমানুষি ছিল। আমাদের প্রধান
প্রধান সাহিত্যিকদের বেলায় তাঁদের মূল্য বিচারে আমরা তাঁদের পশ্চিমি
সাহিত্যিকদের সঙ্গে তুলনা করতাম। মাইকেল আমাদের মিলটন, বঙ্কিম ওয়ালটার স্কট
আর রবীন্দ্রনাথ আমাদের শেলী। এসব তুলনা একেবারেই অবান্তর এমন কথা আমি বলি
না। তবে আপাতদৃষ্ট সাদৃশ্য ছেড়ে দিলে দেখা যাবে অন্তর্গত মিল খুব সুস্পষ্ট
নয়। শেলী এবং রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে মিলটি সর্ব প্রথম উল্লেখযোগ্য সেটি
হলো দুজনের অপূর্ব দেহকান্তি। পুরুষের দেহে এত রূপ সচরাচর দেখা যায় না।
কিন্তু এহ বাহ্য, আগে কহ আর। দেখতে হবে, দুজনের কী মিলেছে কোথায়। শেলী
রবীন্দ্রনাথ দুজনেই প্রেমিক মানুষ যথার্থ প্রেমিক না হলে এরূপ প্রেমের
কবিতা লেখা সম্ভব নয়। সে প্রেম সূক্ষèতম অনুভূতি-জাত প্রেম-রজকিনী প্রেমের
ন্যায় নিকশিত হেম, কামগন্ধ নাহিক তায়। দুইয়ের মধ্যে আরেকটা মস্ত বড় সাদৃশ্য
হলো, দুজনেই কায়-মনোবাক্যে কবি। শুধু লেখনীমুখে কবিতা রচনা করেছেন এমন নয়।
জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে কবি জীবনযাপন করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তবু কাব্যরচনা
ছাড়াও নানাবিধ কাজে লিপ্ত ছিলেন (অবশ্য সেসব সময়েও তাঁকে অ-কবি বলা চলে
না)। শেলী অবশ্য কাব্য রচনা ছাড়া আর কিছুই করেননি- গোটা মানুষটাই কবি।
ইংরেজ
সমালোচক বলেছেন, ‘ঝযবষষবু ঊীযধষবফ াবৎংব ধং ধ ভষড়বিৎ বীযধষবং ভৎধমৎধহপব’ ।
ফুলের সুবাস যেমন নিজের থেকেই নির্গত হয়, শেলীর লেখনীমুখে কবিতা তেমনি
বিনা আয়াসে স্বত উৎসারিত হতো। মিসেস শেলী বলেছেন, এমনও ঘটেছে, শেলী কবিতা
লিখে এনেছেন, বলছেন– লাইনগুলো একের পর এক এত দ্রুত এসে যাচ্ছিল যে, আমি তত
দ্রুত লিখে উঠতে পারছিলাম না। লেখাটা বিষম জড়িয়ে গিয়েছে, এখন পড়তে পারছিনে।
তিন-চারজন মিলে বসে তবে পাঠোদ্ধার করতে হতো। ঝশুষধৎশ নামক কবিতায় শেলী
নিজেই এই স্বত উৎসারিত কাব্যকে বলেছেন– ‘ঢ়ৎড়ভঁংব ংঃৎধরহং ড়ভ
ঁহ-ঢ়ৎবসবফরঃধঃবফ ধৎঃ’। এরূপ স্বতঃনির্গত কাব্য যতই কৃতিত্বের কথা হোক এর
মধ্যে চিন্তা এবং ভাষার কিছু শৈথিল্য থেকে যেতেই পারে। পরবর্তীকালের
সমালোচনায় ওই সব দোষ -ত্রুটি কিছু ধরা পড়েছে। শেলী এবং কিটস একে অন্যের
অনুরাগী ছিলেন। কিটস সে সময়েই মাঝে মাঝে শেলীকে সাবধান করে দিয়ে লিখেছেন-
ণড়ঁ সঁংঃ নব সড়ৎব ড়ভ ধহ ধৎঃরংঃ.
শেলীর কাব্য বুঝতে হলে শেলী মানুষটিকে
আগে বুঝে নিতে হবে। শৈশবাবধি অতিশয় কল্পনাপ্রবণ মন। তার মনগড়া জগতে তার
বাস। ছেলে যেমন কল্পনাপ্রবণ, পিতা শেলী তেমনি কল্পনাবিহীন। তবে অর্থবান
মানুষ ছিলেন। ছেলের লেখাপড়ায় অবহেলা ঘটেনি। সুপ্রসিদ্ধ ঊঃড়হ বিদ্যালয়ে
পাঠিয়েছিলেন ছেলেকে। সেকেলে পাবলিক স্কুলের রীতিনীতি কিছুই বালকের ভালো
লাগেনি। বিশেষ করে ছোট ছেলেদের দিয়ে ‘ফ্যাগ্’ খাটানো দারুণ বিতৃষ্ণার
উদ্রেক করেছিল। ইটনের পাঠ সাঙ্গ করে অক্সফোর্ডে গমন। পড়াশোনার বিস্তীর্ণ
অবকাশ। শেলী বিষম পড়ুয়া ছেলে। সহপাঠীরা বলেছেন, এমন অধ্যয়নস্পৃহা সচরাচর
দেখা যায় না। প্রধান আগ্রহ ফিলসফিতে। বলাবাহুল্য, মনটা শুধুই পুথির পাতায়
নিবদ্ধ ছিল না, নানা কল্পনা-পরিকল্পনায় প্রবৃত্ত ছিল। অচিরে প্রমাণ পাওয়া
গেল। ঞযব হবপবংংরঃু ড়ভ অঃযবরংস – ‘নাস্তিকতার প্রয়োজন’ নামে এক পুস্তিকা
প্রণয়ন করে ছাত্রদের মধ্যে তা বিতরণ করলেন। প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন যে, তিনি
ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না, ধর্ম মানেন না। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ রেগে
আগুন। একীদুর্মতি! বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কারর আদেশ হলো। এখানে বলে নেওয়া
ভালো, এ ব্যাপারেও শেলী জীবনের এক অন্তর্নিহিত বিরোধের প্রকাশ। ঈশ্বরে
বিশ্বাস নেই, ধর্মে বিশ্বাস নেই, একথা ঠিক। ওদিকে আবার শেলীর ন্যায়
ধর্মপ্রাণ মানুষ সংসারে বিরল। জীবনে কোনোদিন কারও অনিষ্ট চিন্তা করেননি।
জীবনীকার বলেছেন– ‘ঝযবষষবু ধিং রহঃবহংবষু ৎবষরমরড়ঁং রিঃযড়ঁঃ ধ ৎবষরমরড়হ’.
অক্সফোর্ড
থেকে বিতাড়িত হয়ে শেলী একেবারে মুক্তবিহঙ্গ। পড়াশোনা করছেন আপন খুশিমতো।
উইলিয়াম গডউইন নামে এক বিপ্লবধর্মী লেখক চড়বঃরপধষ ঔঁংঃরপব নামে একটি গ্রন্থ
রচনা করে মস্ত এক আলোড়নের সৃষ্টি করেছিলেন। ওই গ্রন্থে প্রচারিত মতবাদ
প্রধানত ফরাসি বিপ্লবের মূলতত্ত্ব– শেলীর খুব মনে ধরে গিয়েছিল। গডউইনের
রীতিমতো চ্যালা হয়ে উঠেছিলেন। এক সময়ে ওয়ার্ডসওয়ার্থও গডউইনের দ্বারা খুব
প্রভাবিত হয়েছিলেন। এদিকে ঘরের পাশে ফ্রান্সে বিপ্লব, ইংল্যান্ড শশাব্যস্ত।
ভয় পাছে বিপ্লবের ঢেউ ইংল্যান্ডের তটে এসে আছড়ে পড়ে। শাসকগোষ্ঠী
শাসনযন্ত্রটিকে ধরেছেন শক্ত হাতে। নানাবিধ বিধিনিষেধ জারি করেছেন, কারও
ট্যা-ফো করার জো নেই। ম্যাঞ্চেস্টার ল্যাঙ্কাশায়ারের শ্রমিকরা তাঁদের
নানাবিধ দাবিদাওয়া নিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছিল। সরকার সৈন্য লাগিয়ে
নির্বিচারে গুলি চালিয়ে বহু লোক হত্যা করল। শেলী ক্রোধে, ঘৃণায় ক্ষিপ্ত।
লিখলেন জোর কলমে এক কবিতা। দেশবাসীকে ডেকে বললেন-
জরংব ষরুশব ষরড়হং ধভঃবৎ ংষঁসনবৎ
ওহ ঁহাধহয়ঁরংযধনষব হঁসনবৎ-
ঝযধশব ুড়ঁ পযধরহং ঃড় বধৎঃয ষরুশব ফবি
ডযরপয রহ ংষববঢ় যধফ ভধষষবহ ড়হ ুড়ঁ
ণব ধৎব সধহু-ঃযবু ধৎব ভব.ি
কবিতা
হিসেবে উঁচু দরের কিছু নয়। প্রথম যৌবনে গডইন-প্রভাবে মনে যে উত্তেজনার
সৃষ্টি হয়েছিল, এ তারই নিদর্শন। মন ক্রমেই শান্ত হয়ে এসেছে। এরূপ উঁচু গলায়
কথা পরে খুব কমই বলেছেন। প্রতিশোধস্পৃহার মধ্যে অন্যায়ের প্রতিবিধান
খোঁজেননি। ঘৃণা-বিদ্বেষ শেলীর স্বভাববিরুদ্ধ। বেশিরভাগ সময়েই নিজেকে
প্রকাশ করেছেন বিনয়নম্র বচনে। বিপ্লবী মানুষ হয়েও ঘৃণা-বিদ্বেষের বিরুদ্ধে ই
তাঁর অভিযান। তিনি প্রেমিক মানুষ, প্রেম বিলিয়েছেন, বিদ্বেষ ছড়াননি।
প্রেমের অভাবেই মনুষ্যসমাজে এত অশান্তি। মানুষ একে অন্যকে যথেষ্ট পরিমাণে
ভালোবাসে না বলেই সংসারে এত অবিচার-অত্যাচার। বলি বটে, শেলী বিপ্লবী কবি।
কিন্তু বিপ্লব বলতে স্থূলের চাইতে সূক্ষেèার দিকেই তাঁর নজর ছিল বেশি।
‘বাস্তিল’ ধ্বংস করলেই বিপ্লব হয় না। ধ্বংস করতে হবে মানুষের মনে বহু যুগ
ধরে যেসব ধ্যানধারণা, সংস্কার বিশ্বাস পুঞ্জভূত হয়ে আছে সে সবকে। মনের
অন্ধকার দূর করতে হবে। ঙফব ঃড় ঃযব ডবংঃ ডরহফ নামক কবিতায় বলছেন– গধশব সব
ষুৎব বাবহ ধং ঃযব ভড়ৎংঃ রং– ঝড়কে উদ্দেশ করে বলছেন, তুমি বনের ভিতর দিয়ে
যেমন ভীমবেগে প্রবাহিত, তেমনি প্রবলবেগে আমার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে আমার
বাণীকে তুমি প্রচার কর– আমার মনোবসনা, আমার আশা-আকাক্সক্ষা, আমার জীবনাদর্শ
তুমি ঝড়ের বেগে পৃথিবীময় ছড়িয়ে দাও। সেই বীজ থেকে পৃথিবীতে এক নতুন
মানবসমাজের সৃষ্টি হবে। বলেছেন– ‘ইব ঃযৎড়ঁময সু ষরঢ়ং ঃড় ধধিশবহবফ /ঞযব
ঃৎঁসঢ়বঃ ড়ভ ধ ঢ়ৎড়ঢ়যবপু’। বিপ্লব বলতে শেলী বুঝেছেন– মনের অন্ধকার দূরীকরণ,
সকল প্রকার বন্ধন মোচন, নতুন সৃষ্টির বীজ বপন।
শেলীর চরিত্রে খুব
লক্ষণীয় কিছু, বৈশিষ্ট্য ছিল। সারাক্ষণ মনে একটা অস্থিরতা, কী যে চান নিজেই
জানেন না, যা পান তা চান না। এই মনটাকে রবীন্দ্রনাথ চেনেন, তিনি তাকে ভাষা
দিয়েছেন- ‘যা না চাইবার তাই আজি চাইগো, যা না পাইবার তাই কোথা পাইগো।
‘মনের এই অতৃপ্তি নিয়েই শিলীর জীবন। ওয়েস্ট উইন্ড কবিতায় যেমন দেখা যায়,
ঝড়ের গতিবেগ তাঁকে মাতিয়ে তুলেছে, নিজের জীবনটিও তেমনি ঝটিকা বেগে ছুটেছে
এবং অতি স্বল্পকালেই নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। মাত্র তিরিুশ বছরের জীবন। কোনো
কিছুই রয়েসয়ে ধীরেসুস্থে করার অবকাশ পাননি, যেন জানাই ছিল হাতে বেশি সময়
নেই, বিলম্ব সইবে না। বয়স যখন মাত্র উনিশ তখনই হ্যারিয়েট ওয়েস্টব্রক নামের
এক তরুণীকে বিয়ে করে ফেললেন। পরপর দৃষ্টি সন্তানও হয়ে গেল। দুজনে সুখেই
ছিলেন; কিন্তু হ্যারিয়েট সন্তানদের তেমন যত্ন নিতেন না। শেলী শিশু দুটিকে
খুবই ভালোবাসতেন। শিশুদের দেখাশোনা নিয়েই স্বামী-স্ত্রীতে খিটিমিটি লেগে
থাকত। অশান্তির সৃষ্টি হলো, ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। পরে হ্যােিয়ট আত্মহত্যা
করেছিলেন। শেলী শিশু দুটির ভার নেওয়ার জন্য কোর্টে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন।
সে প্রার্থনা মঞ্জুর হয়নি। বিচারক বলেছিলেন, আবেদনকারী এমন এক আত্মভোলা কবি
মানুষ যে, শিশু সন্তানদের তত্ত্বাবধান করার মতো যোগ্যতা তাঁর নেই। এটাও
একটা মনোবেদনার কারণ হয়েছিল।
ইতোমধ্যে গডউইন পরিবারের সঙ্গে শেলীর খুবই
ঘনিষ্ঠতা জন্মেছে। নিত্য যাওয়া-আসা। গডউইন-কন্যা মেরির সঙ্গে খুব ভাব
জমেছে। অনতিকাল পরে দেখা গেল মেরি এবং শেলী কাউকে কিছু না বলে পালিয়ে গিয়ে
বিয়ে করেছেন। গডউইন মানুষের অবাধ স্বাধীনতার মহান প্রচারক। কন্যা-জামাতার
ব্যবহারে বিরক্তি বোধ করে থাকলেও প্রকাশ্যে কিছু বলতে পারেননি। পরিচিত মহলে
অবশ্য শেলী কিছু নিন্দাভাজন হয়েছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন মেরি গডউইনের প্রতি
শেলীর অনুরাগই হ্যারিয়েটের অকালমৃত্যুর কারণ। পরে অবশ্য জানা গিয়েছিল যে,
হ্যারিয়েটের মৃত্যুর জন্যে হ্যারিয়েট নিজেই দায়ী। এই সূত্রে বলে নেওয়া ভালো
যে, শেলী প্লেটনিক প্রেমের পক্ষপাতী ছিলেন। একনিষ্ঠাতা সে প্রেমের বিশিষ্ট
লক্ষণ নয়। অবশ্য সে প্রেম দেহগত নয়, মনোজাত। যাকে আমার মনে ধরেছে তাকে
ভালোবাসার অধিকার আমার আছে, এই ছিল তাঁর বিশ্বাস।
পত্নী মেরিসহ জীবনের
শেষ কয়টি বছর কাটিয়েছেন ইটালিতে। কেন জানি না, ইটালিকে বলেছেন– ‘চধৎধফরংব
ড়ভ বীরষবং’ বা নির্বাসিতের স্বর্গ। বোধ করি ভেবেছিলেন, ইংল্যান্ডে যা
পাননি, ইটালিতে তাই পাবেন। তাঁর বিপ্লবী অশান্ত মনকে শান্ত করার মতো খুব যে
কিছু ইটালিতে পেয়েছিলেন এমন মনে হয় না। তবে এখানেও আবার এক নতুন প্রেম
তাঁর চিত্তকে দোলায়িত করেছিল। এমিলিয়া ভিভিয়ানি নামের এক ইটালীয় তরুণীর
প্রেমে পড়েছিলেন। ঊঢ়রঢ়ংুপযরফরড়হ কাব্যটি এই প্রেমকাহিনিকে আশ্রয় করে রচিত।
স্পষ্টতই বলেছেন– ঊসরষু, ও ষড়াব ঃযবব। একটু চাতুরীর আশ্রয় নিয়েছিলেন।
ভূমিকায় বলেছিলেন, এটি তাঁর এক বন্ধুর কাহিনি। বলা বাহুল্য, সে কথায় কেউ
ভোলেননি। কিন্তু সে প্রেম যে একান্ত বিদেহী প্রেম তা স্পষ্টত প্রতীয়মান।
শেলীকৃত এমিলিয়ার বর্ণনা– ঝবৎধঢ়য ড়ভ ঐবধাবহ, ঃড়ড় মবহঃষব ঃড় নব যঁসধহ, আবার
বলেছেন– ঝযব রং ধ ংরংঃবৎ, ধ াবংঃধষ ংরংঃবৎ, ৎধঃযবৎ ঃযধহ ধ সরংঃৎবংং।
শেলীর
প্রেম যেমন মনগড়া, যে জগতে বাস করেছেন সে জগৎটিও তাঁর মনগড়া। আগেই বলেছি
চাওয়ায় আর পাওয়ায় মিল ঘটেনি। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়-‘যাহা চাই তাহা ভুল করে
চাই, যাহা পাই তাহা চাই না।’ এ মানুষ সুখী হতে পারেন না, শেলী সুখী মানুষ
ছিলেন না। বাস্তবিকপক্ষে কোনো আদর্শবাদী মানুষই সুখী নন। তাঁরা সর্বক্ষণ
কিছু একটার অভাব বোধ করেন, অন্তরের একটা ব্যর্থতার ব্যথা লেগেই থাকে। এঁদের
অভাব কখনো ঘুচবার নয়; কেননা তাঁরা যা চান তা পাওয়ার অতীত। শেলী নিজের
ভাষাতেই তা প্রকাশ করেছেন-
ঞযব ফবংরৎব ড়ভ ঃযব সড়ঃয ভড়ৎ ঃযব ংঃধৎ.
ঙভ ঃযব হরমযঃ ভড়ৎ ঃযব সড়ৎৎড়ি
ঞযব ফবাড়ঃরড়হ ঃড় ংড়সবঃযরহম ধভধৎ
ঋৎড়স ঃযব ংঢ়যবৎব ড়ভ ড়ঁৎ ংড়ৎৎড়.ি
দুনিয়াটা
যেমনভাবে চললে খুশি হতেন, ঠিক সেভাবে চলছে না দেখে সর্বক্ষণ মনে একটা
অশান্তি। ব্যর্থতাজনিত মনে একটা বিষাদের ভাব। বিষাদ রোমান্টিক কাব্যের একটা
বিশেষ লক্ষণ। আশাভঙ্গে দুঃখকে রোমান্টিক কবি অনেক বেশি বাড়িয়ে দেখেছেন।
শেলীর স্পর্শকাতর মনে বিষাদের ভাবটা ক্রিয়া করেছে একটু অত্যধিক পরিমাণে।
বিশেষ করে আদর্শবাদী মানুষকে আশাভঙ্গের আঘাত পেতে হয় প্রতি পদে। হতাশাজনিত
মর্মপীড়া প্রকাশ পেয়েছে শেলীর অনেক কবিতায়। মনে হতে পারে একটু যেন
ছিঁচকাঁদুনে ভাব– ‘ও ঢ়ধৎঃ, ও ংরহশ, ও ঃৎবসনষব, ও বীঢ়রৎব!’ এ জাতীয় কান্না
অনেক কবিতায়। তবে এই যে, দুনিয়াটাকে নিজের মনের মতো করে গড়ে তুলতে পারছেন
না, তাই নিয়ে দুনিয়াসুদ্ধ লোকের সঙ্গে ঝগড়া করতে বসেননি। দোষ দিয়েছেন
নিজেকেই, নিজের অক্ষমতাকেই। ইংরেজিতে যাকে বলে ঝবষভ-ঢ়রঃু, বলা যেতে পারে
আত্ম-ধিক্কার, এ তাই। নিজেই নিজেকে কৃপার চক্ষে দেখেছেন। লক্ষ করার বিষয়,
সচরাচর যা ঘটে থাকে– অক্ষম রোষ অনেক সময় ধ্বংসাত্মক রূপ নেয়– শেলীর বেলায়
তা ঘটেনি। কখনো বলেননি, ভেঙেচুরে সব সাবাড় করে দাও। ভাঙনের গান কবি ভ্রাতার
জন্য সকল কবি মিলে অশ্রু বিসর্জন করছেন, শেলী তাঁদের অন্যতম। নিজের বর্ণনা
দিচ্ছেন– ‘অ ঢ়যধহঃড়স ধসড়হম সবহ, পড়সঢ়ধহরড়হষবংং’। শেলী ও কিটস দুজনেই চলে
গিয়েছেন সেই কবে। আজ দুশো বিশ বছর পরে রোমান্টিক কবি হিসেবে আমরা শেলী ও
কিটসকে স্মরণ করি এক সঙ্গে, দুজনের নাম উচ্চারণ করি এক সঙ্গে যেন দুই সহোদর
ভ্রাতা।
মনে হয় শেলীর মনে মৃত্যুর একটা ঢ়ৎবসড়হরঃরড়হ ছিল। তা না হলে
নানা কবিতায় নানা ভাবে মৃত্যুর কথা অত করে বলবেন কেন। এমন নয় যে দীর্ঘকাল
ধরে রোগে ভুগছেন কিংবা কিটসের ন্যায় মারাত্মক রোগে আক্রান্ত। স্বাস্থ্যবান
সুদর্শন পুরুষ, তিনি কেন বলবেন– ঙ ড়িৎষফ! ঙ ষরভব ! ঙ ঃরসব ঙহ যিড়ংব ষধংঃ
ংঃববঢ়ং ও পষরসন.
মাত্র তিরিুশ বছর বয়সে মৃত্যু, তাও আকস্মিক দুর্ঘনাটায় জলে ডুবে। কাজেই তার এ মৃত্যুচেতনা একটু বিস্ময়কর ঠেকে।
শেলী
দীর্ঘকাল কিছু কাব্যগ্রন্থ এবং নাটক রচনা করেছেন কিন্তু লিরিক বা গীতি
কবিতা রচয়িতা হিসেবেই সমধিক পরিচিত। তাঁর দীর্ঘতর কাব্যসমূহও খানিকটা
লিরিক্যাল বা গীতধর্মী। এদিক থেকে তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনীয়।
রবীন্দ্রনাথ বহুবিধ জিনিস লিখেছেন কিন্তু সাধারণ পাঠকরা তাঁকে প্রধানত
লিরিক এবং সংগীত রচয়িতা হিসেবেই জানে। বাঙালি মনের কাছে শেলী-কাব্যের বিশেষ
করে তাঁর লিরিক সমূহের একটা গভীর আবেদন আছে। ভাবাবেগপূর্ণ তাঁর কবিতা
বাঙালি মনে আজও যথেষ্ট সাড়া জাগায়। অবশ্য মনে রাখতে হবে যে শেলী মানুষটি
ছিলেন ইনটেলেকচুয়াল স্বভাবের। বিদ্যাবত্তাও ছিল প্রচুর! তাঁর কবিতায় শুধু
ভাবাবেগ নয়, ভাববার কথাও যথেষ্ট থাকত। সেখানেও তিনি বাঙালি মনকে ছুঁয়েছেন।
কাব্যকে
ছাড়িয়ে কবি। কীর্তির চাইতে কর্তা মহৎ। শেলীর কাব্য বড়, কিন্তু কবি শেলী
মানুষটি তার কাব্যের চাইতেও বড়। যে মানুষ সৌন্দর্যের সৃষ্টি করেছেন সে
মানুষের মন যে কত সুন্দর, যিনি অসম্ভবের স্বপ্ন দেখেছেন, উচ্চতম আদর্শে
কামনায় আপন সুখ বিসর্জন দিয়েছেন সে মানুষ যে কত মহান, শেলীর জীবন তারই
নিদর্শন।
